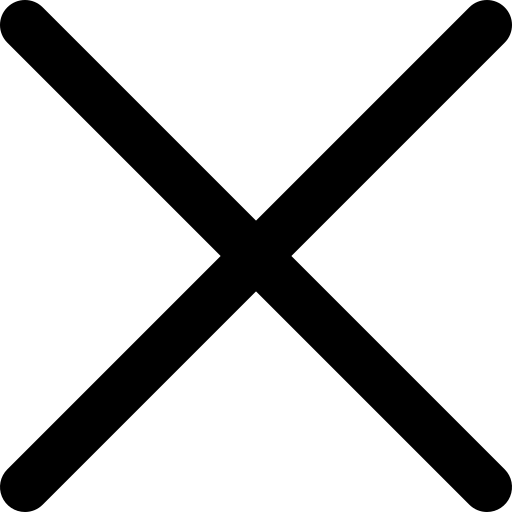আমির সুহাইল ওয়ানি
ভারতীয় সভ্যতার এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তার সমন্বয়, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের ক্ষমতা। এই চিত্তাকর্ষক মানসিকতার অন্যতম উজ্জ্বল প্রতীক হল 'গঙ্গা–যমুনি তেহজিব', উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক ভূগোল থেকে আগত একটি শব্দ, যেখানে গঙ্গা এবং যমুনা নদী পাশাপাশি প্রবাহিত। সময়ের সাথে সাথে এই শব্দটি কেবল একটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ধারা নয়, বরং এমন এক বিস্তৃত জীবনদর্শনের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য, এবং অন্যান্য ভারতীয় আধ্যাত্মিক প্রবাহ, পরস্পরকে প্রভাবিত করে এক সমন্বিত সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, যা তার প্রতীকচিহ্ন, নন্দনবোধ, ভাষা, ভক্তি ও দৈনন্দিন আচার-আচরণে অনন্য।
এটি কোনো মতবাদ নয়, বরং এক জীবন্ত অভিজ্ঞতা, যেখানে বৈচিত্র্যকে ভয় না করে তাকে আপন করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়; যেখানে বিভিন্ন ধর্ম নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও মানবিক ও সূক্ষ্ম উপায়ে একে অপরকে সমৃদ্ধ করেছে। গঙ্গা–যমুনি তেহজিব মূলত আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দাঁড়ানো এক সমন্বিত কল্পনা, যা কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দৈনন্দিন সহাবস্থান, বাণিজ্য, তীর্থযাত্রা, শিল্পচর্চা, আর্থসামাজিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে এটি স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে।
পণ্ডিত, ধর্মতাত্ত্বিক বা শাসকদের তুলনায় সাধক, কবি, গায়ক, কারিগর ও সাধারণ মানুষই এই সংস্কৃতি গঠনে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছেন। ভক্তি ও সুফি ধারাই এ পরিবেশকে লালন করেছে। উভয়েই ঈশ্বরপ্রেমকে কঠোর নিয়মের ঊর্ধ্বে রেখেছে; অন্তরের পরিবর্তনকে বাহ্য পরিচয়ের চেয়ে মূল্যবান জেনে এসেছে; এবং সংকীর্ণতার পরিবর্তে করুণাকে মানবিকতার বিস্তৃত পরিসরে উন্নীত করেছে। কবিরের মতো সাধক সরল ভাষায় সংকীর্ণ ধর্মীয় অনুশাসনের সমালোচনা করেছিলেন এবং এমন এক ঈশ্বরচেতনার কথা বলেছিলেন যা কোনো লেবেল মানে না। উত্তর ভারতের সুফি দরগাহগুলোও সব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল; তাদের মাজারে মানুষের মিলন ঘটত ভক্তির এক সাধারণ ভিত্তিতে।
এই মেলবন্ধনের ছাপ স্পষ্ট ভাষা, শিল্প, সংগীত, স্থাপত্য ও সামাজিক রীতিতে। হিন্দুস্তানি ভাষা উদ্ভূত হয়েছে সংস্কৃত–প্রাকৃত–ফারসি–আরবি–তুর্কি প্রভাবের সম্মিলনে। গজল, ভজন, কওয়ালি, মারসিয়া, যে ধারাই হোক না কেন, এক বিশেষ যৌথ নন্দনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। খেয়াল, ঠুমরি ইত্যাদি সঙ্গীতরূপে হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীরা পাশাপাশি সৃষ্টির কাজে যুক্ত ছিলেন। ফারসি সুরধারা ভারতীয় রাগকে নতুন রূপ দিয়েছিল; মুসলিম কবি কৃষ্ণভক্তি রচনা করেছেন, আবার হিন্দু গায়ক সুফি কালাম পরিবেশন করেছেন, এ এক গভীর সাংস্কৃতিক স্রোত।
স্থাপত্যেও এই সমন্বয় দৃশ্যমান। দিল্লি, আগ্রা, লখনউ, লাহোরের ইন্দো–ইসলামিক স্থাপত্যে স্থানীয় কারুকার্য ও ফারসিয়ান নকশা এক অভূতপূর্ব রূপ সৃষ্টি করেছে। গম্বুজ, খিলান, জালি, ক্যালিগ্রাফি, সব মিলিয়ে এমন রূপ ফুটে উঠেছে যা সম্পূর্ণ বিদেশি নয়, আবার নিছক দেশীয়ও নয়, বরং এক স্বতন্ত্র ভারতীয় মেলবন্ধনের পরিচয়। উদ্যান, মসজিদ, মন্দির, সারাই, হাভেলি, সবই বহু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাপনে স্থান করে নিয়েছিল।
আরো গভীর ছিল দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই মিলন। উৎসব সামাজিকভাবে ধর্মভেদ অতিক্রম করে উদ্যাপিত হতো। প্রদীপ জ্বালানো, মিষ্টি বিনিময়, সুফি দরগার উরস, ধর্মীয় উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময়, সব ছিল সাধারণ জীবনরীতির অংশ। রান্নার ধারা স্থানীয় উপাদান ও মধ্য এশীয় পদ্ধতির মিলনে নতুন খাদ্যরীতি সৃষ্টি করেছিল। পোশাক, অভিবাদন, রসিকতা, সবই বহু উৎস থেকে প্রভাব নিয়ে মানুষের পরিচয়কে নমনীয় করে তুলেছিল।
আধ্যাত্মিকভাবে, গঙ্গা–যমুনি মানসিকতা সত্যের বহু রূপকে এক মর্মে দেখার শিক্ষা দিয়েছে। বিশ্বাসের পার্থক্য থাকলেও তা বৃহত্তর শ্রদ্ধাবোধের ভেতরে স্থাপন করা হতো। মানুষ দয়ালু হয়ে উঠত, কারণ ঈশ্বরিক সত্য কোনও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। অনেকে মন্দির ও দরগাহ উভয়ই দর্শন করতেন, বিভ্রান্তি থেকে নয়, বরং ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্র অনুভবের আস্থায়। এই ধারার কবিতায় প্রায়ই প্রিয়তমের এমন রূপক পাওয়া যায় যা মতবাদভিত্তিক ব্যাখ্যা এড়িয়ে অন্তর্দর্শনকে আহ্বান করে।
ইতিহাসে কিছু অঞ্চল বিশেষভাবে এই সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠেছিল। লখনউসহ আওধ ছিল রুচি, সাহিত্যচর্চা ও আচার–ব্যবহারের এক অনন্য কেন্দ্র। দাক্ষিণাত্যেও ভারতীয় ও পারসীয় প্রভাবের সুসমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারা প্রকাশ পেয়েছিল। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, বাংলা ও গুজরাটেও ভক্তিধারার গভীর মিলন লক্ষ্য করা যায়। এসব অঞ্চলে এই সংস্কৃতি কোনো তাত্ত্বিক প্রচার থেকে নয়, বরং মানুষের প্রতিদিনের সহাবস্থান থেকেই স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল। এই সংস্কৃতি টিকে আছে কারণ এটি সাধারণ মানুষের জীবনে প্রোথিত। মায়েদের লোরি, কারিগরদের সম্মিলিত কাজ, কৃষকদের মৌসুমি রীতি, শিল্পীদের মিলিত পরিবেশনা, এসবই তা বহন করেছে। লোককথা, ভাষা, স্মৃতি, আচার, সবেতেই তার স্থায়িত্ব।
তবু আধুনিক সময়ে এই সূক্ষ্ম সংস্কৃতির পরিবেশ কোথাও কোথাও ভঙ্গুর। দ্রুত নগরায়ণ, সামাজিক দূরত্ব, বৈশ্বিক একরূপীকরণ, সব মিলিয়ে স্থানীয় সহাবস্থানের ধারা দুর্বল হতে পারে। কঠোর পরিচয়বোধ বহুস্তরীয় পরিচয়কে আড়াল করে দেয়। ক্ষতি শুধু সামাজিক নয়, আধ্যাত্মিকও। এই ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন মানে অতীতকে পূজো করা নয়, বরং এমন সম্পদ পুনরাবিষ্কার করা যা পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলে। সাহিত্য, সঙ্গীত, ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য এগুলো মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। খুসরোর কবিতা, কবিরের বাণী, মীরার ভজন, দারা শিকোর দর্শন, সবই মানুষকে সীমানার ওপারে নিয়ে যায়।
প্রতীকী ছবি
আধ্যাত্মিক সংলাপ, পরস্পরের উপাসনালয়ে ভক্তিভরে উপস্থিতি, শিল্পের সহযোগিতা, এসবই ঐতিহাসিক সমন্বয়ের ধারাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে পারে। আঞ্চলিক ভাষা, কারুশিল্প, লোকসংস্কৃতি বাঁচানো খুব জরুরি; এগুলো হারালে সমন্বয়ের অভ্যাসও হারিয়ে যায়। পরিবার ও স্থানীয় সমাজই এর প্রকৃত রক্ষক।অবশেষে, গঙ্গা–যমুনি তেহজিব এমন এক আধ্যাত্মিক মানবদর্শন, যেখানে বৈচিত্র্য বিভাজন নয়, প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটায়। গঙ্গা ও যমুনা মিলেও নিজেদের হারায় না; বরং বৃহত্তর, উর্বর স্রোত সৃষ্টি করে। ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমন, স্বাতন্ত্র্য রেখে পারস্পরিক সমৃদ্ধিতে বিকশিত।
আজকের বিভাজনমুখী পৃথিবীতে এই ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেয়, মৃদুতা, কৌতূহল ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা দুর্বলতা নয়, বরং এক সভ্যতার পরিপক্কতা। তাই গঙ্গা–যমুনি তেহজিবকে পুনর্জীবিত করা শুধু সাংস্কৃতিক প্রকল্প নয়, আধ্যাত্মিক প্রয়োজন। এর ধারাবাহিকতা টিকে থাকবে প্রতিদিনের ছোট ছোট দয়া, সহযোগিতা ও উন্মুক্ততার মধ্যে, যা ভারতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অন্তঃসলিলা সুর হয়ে বয়ে চলবে।